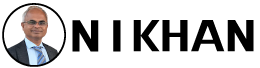তিন হাজার বছর আগে একটা নদী প্রবাহিত হতো। পদ্মার মূল প্রবাহের বিশাল স্রোতধারা এই নদী দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছাতো। তখনকার নাম জানা না থাকলেও এখন তার নাম কপোতাক্ষ। তখন অসংখ্য বাঘ, মহিষ, হরিণ, বন গরু, বড় বড় অজগর, গোখরো সাপ বিচিত্র জীব জন্তুতে নদীর দু’পাড়ের জঙ্গল ভরপুর ছিল। এই স্রোতধারা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে থাকে। অপরদিকে নড়াইলের চিত্রা ও কামারখালী মধুমতি স্রোতধারা বেগবান হয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এছাড়া অসংখ্য শাখা নদী ও উপনদী জাল বিস্তার করেছিলো। এরপর মেঘনার সাথে পদ্মা সংযুক্ত হয়। কপোতাক্ষের ক্ষীণ প্রবাহে বাক সৃষ্টি হয়। দুই বাক একসাথে মিলে লুপ তৈরি করে তার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকে। এমনই একটি লুপের একপাশে পলি পড়ে নদী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাওড়ের সৃষ্টি। খাজুরা ও ঝাপার বাওড় এমনিভাবে পাশাপাশি সৃষ্টি। নিকটতম স্থানে দুই বাওড়ের মাঝের দূরত্ব এক কিলোমিটার। এখনো বাওড়ের এপাড় থেকে ওপাড়ের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। এ থেকে সেই সময়কার নদীর প্রবাহ অনুমান করা যায়। এই বাওড়কে অশ্বক্ষুরাকৃতি লেক বলে। যশোরে এরকম অন্তত ২৭টি বাওড় তৈরি হয়েছে।

খাজুরা বাওড়, ১২ নভেম্বর ২০১৭ দোতালার বারান্দা হতে
ঝাপা ও খাজুরার বাওড়ের নিকটতম স্থানে বর্তমান মনিরামপুর থানার অধীনে বউনিয়া গ্রাম গড়ে উঠেছিল। এই গ্রামেই এন আই খানের বংশধরেরা বসতি স্থাপন করে। জানা যায় ময়মনসিংহ থেকে প্রথমে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার মৌতলা এলাকায় বসতি স্থাপন করে। সেই সময়ের সুন্দরবন এলাকা। এখন সুন্দরবন আরো দূরে সরে গেছে। কী কারণে সেখান থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল তা জানা যায় না। হতে পারে বাহাদুর শাহের পতনের পর অনেকে দিল্লী ছাড়তে হয়েছিল। কেউ প্রাণভয়, কেউবা সুযোগের সন্ধানে। দিল্লি থেকে প্রথম ময়মনসিংহ তারপর সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার মৌতলা, এরপর বউনিয়াতে বসতি। সে সময় এখানে বাঘ আর সাপের রাজত্ব, তবে মাছের প্রাচুর্য মানুষকে আকর্ষণ করেছে। দুটি বাওড়ের দু’পাশের জমি বেশ উর্বর, সেটি একটি কারণ হতে পারে। তার চেয়ে বড় কারণ এই গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই মির্জাপুরে তৎকালীন যশোরের হেডকোয়ার্টার বা সদর দপ্তর ছিল। তখনকার দিনে যশোর খুলনা ফরিদপুর এবং কুষ্টিয়া একত্রে ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং কর্মসংস্থানের আকর্ষন এখানে আসার কারণ। সম্রাট আকবরের সময় বাংলার সুবাদার শাহ শুজার শ্যালকপুত্র মির্জা সফসিকান ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে যশোরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তার নাম অনুসারে এই স্থানের নাম মির্জানগর করা হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর মির্জানগর ইংরেজদের কাছে শত্রুভাবাপন্ন এলাকা তাই জেলা হেডকোয়ার্টার বর্তমান যশোর জেলা সদরে নিয়ে যায়।
একদিন জমিদার বর্তমান বউনিয়ার তহসিলদারকে খোঁজ করলেন। কিন্তু পেলেন না, কদিন পর তহসিলদারের সাথে দেখা হল। তহসিলদার বলল হুজুর আমি আপনার বউনিয়াতে গিয়েছিলাম। আপনার বউনিয়া শুনে জমিদার মনে মনে বিরক্ত হলেন। ভাবলেন এই গ্রামের নাম আর বউনিয়া রাখা যায় না। যে কথা সেই কাজ, জমিদার বউনিয়া গ্রামে আসলেন দেখলেন কালিতলায় একটা মহিষ বলি দেয়া হচ্ছে। ব্যাস পেয়ে গেলেন, নাম হবে মহিশেশ্বর নগর। স্থানীয় মানুষ মহিশেশ্বর নগরকে মশ্বিমনগর করে নিয়েছে।
এই মশ্বিমনগরে ১৯৫৬ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি উত্তরের একটা খড়ের চৌরী ঘরে মো. নজরুল ইসলাম খানের জন্ম। বাবা ইনসান আলী খান চার ভাই চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দাদা আশরাফ আলী খান তার বাবার একমাত্র পুত্র। পেশায় কৃষিজীবী ছিলেন। হাইস্কুল পর্যন্ত তার পড়াশোনা। তবে ভালো ইংরেজি জানতেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন। মা আয়েশা খাঁন দুই মায়ের প্রথম পক্ষের তিন ভাই দুই বোন দ্বিতীয় পক্ষের তিন ভাই চার বোন মোট ১২ ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের সবচেয়ে বড়। প্রাইমারি স্কুলের বাইরে যেতে পারেননি। মায়ের বাবা আমজাদ আলী খান। তার বাবা আলিজাদ খানের একমাত্র সন্তান। নানার পূর্বপুরুষেরা প্রভাবশালী সরকারি চাকরি করতেন। নানার পূর্বপুরুষ মোবারক খানের নাম অনুসারে গ্রামের নাম মোবারকপুর। নানা ফর্সা লম্বা সুপুরুষ ছিলেন। বড় নানি কপোতাক্ষের পাড়ের দেয়াড়া গ্রামের, ফর্সা তবে মোঙ্গলদের মত চেহারা। বড় নানী পর দ্বিতীয় নানি অর্থাৎ আমার নানী কে বিয়ে করেছেন। ছোট নানী তার বাবার একমাত্র সন্তান। নানী কপোতাক্ষ পাড়ের দেয়াড়া গ্রামের। নানার বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। নানী শ্যাম বর্ণের। তবে বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় আদরের দুলালী ছিল। সরল সহজ নানী প্রথম পক্ষের সন্তানদের খুবই স্নেহ করতেন । তাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমি উভয় পক্ষের মামা খালাদের মিলেমিশে থাকতে দেখেছি। বড়দের কথা ছোটদের বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিতে দেখেছি। আমাদের বাড়ি থেকে মামার বাড়ি চার কিলোমিটার দূরে। নানারা প্রভাবশালী ছিলেন তাই বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অবিবাহিত একমাত্র সন্তানের সাথে বিয়ে সম্ভব হয়েছিল।
নানা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথে মিলে রাজগঞ্জে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেছিলেন। আমি সেখান থেকে ১৯৭২ সালে এসএসসি পাশ করেছি। মায়ের কাছে গল্প শুনেছি, মায়ের বিয়ে হওয়ার পর আমার দাদার প্রতিবেশীরা রাজগঞ্জ বাজারে হলুদ বিক্রি করতে যেত। হলুদ বিক্রি করা খুব একটা সম্মানের কাজ না বলে মনে করা হতো। নানা একবার লোক দিয়ে নিষেধ করে দিয়েছে হলুদ না বিক্রির জন্য। তাদের রুটি-রুজির ব্যাপার তাই তারা শুনবে কেন? নানার সেটা চিন্তা করার সময় নেই? মানুষের মনে করবে ছোট বংশের লোকদের গ্রামে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। তাই একদিন রাজগঞ্জ বাজারে আমাদের পাড়ার সবার হলুদ ফেলে দিয়েছিল। এরকম আরো বেশ কিছু কাহিনী আছে।
৪৭ বছর বয়সে নানা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অসহায় ছেলে মেয়েদের রেখে অল্প বয়সে ইন্তেকাল করার জন্য লেখাপড়া বেশি দূর এগোতে পারেনি। সবাই স্কুলে পড়াশোনা করতেন মৃত্যুর পর দুইজন ম্যাট্রিক ও অপরজন ডিগ্রি করে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছে। মায়ের আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। নানা মারা যাওয়ার আগে অল্প বয়সে মায়ের বিয়ে দিয়ে গেছে। ১৯৫৬ সালে দেশে অভাব ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা চলছিল। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে বরিশাল খুলনাসহ অন্যান্য জেলায় দুর্ভিক্ষের তথ্য পাই। মায়ের কাছে শুনেছি যশোরে খাদ্যাভাব ছিল। মায়ের বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীর প্রতিবেশীদের পেঁপে খেয়ে দিন যাপন করতে দেখেছে। দাদার যথেষ্ঠ জমিজমা ছিল যা বাপ-চাচাদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়েছে। কিন্তু কেন তাদের অভাব ছিল সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এখনকার মতো তখন উচ্চ ফলনশীল ধান ছিল না। জীবজন্তুর উপদ্রব ছিল। আমরা নিজেও দেখেছি হাজার হাজার বাবুই পাখিসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি ধান পাকার আগেই খেয়ে নিত। আমি নিজে দেখেছি বাঁশ দিয়ে ফটফটি তৈরি করা হতো। ২০-২৫ ফুটের একটি বাশ ধানক্ষেতে পুঁতে মাথা চিরে অর্ধেক পাশে দড়ি বেধে টং পর্যন্ত নেয়া হতো। দড়ি টেনে ছেড়ে দিলে বাকী অর্ধেক বাশের সাথে বাড়ি লেগে ফট ফট শব্দ হতো। কখনো কখনো দড়ির সাথে একটা টিন বাঁধা থাকত। দড়ি টান আর ঢিল দিলেই বাঁশের গায়ে টিনে আঘাত লেগে শব্দ হতো। টিন আর ফাটা বাঁশের শব্দে পাখি পালিয়ে যেত। সেই সময়ে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় সাড়ে চার কোটি মানুষ ছিল। তারপরও উন্নত মানের বীজ এবং চাষের অভাব ছিলো। সরকার থেকে তেমন একটা নজর দেয়া হতো না বা সামর্থ ছিল না।
বাওড়ের পাড়ে মনোরম পরিবেশে আমাদের বাড়ি ছিল। পাড় দিয়ে জঙ্গল ছিল সেখানে প্রচুর সাপ ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বন বিড়াল বাড়ির পাশে বাওড়়ের তীরে জঙ্গলে এসে তাক করে উঠানের মুরগির ধরতো। গুইসাপ ভাঙ্গা বেড়া দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে তাওয়া থেকে মুরগির ডিম ও বাচ্চা খেয়ে ফেলতো। আকাশে চিল ছো দিয়ে মুরগির বাচ্চা ধরে নিয়ে যেত। উঠানের পাড়ে বালি বালি মাটিতে কচ্ছপ ডিম পেড়ে যেত। প্রাইমারি স্কুলে third স্যার মনমথ নাথ চক্রবর্তী কচ্ছপের ডিম খুব পছন্দ করতেন। তার সাথে খাতির রাখার জন্য কচ্ছপের ডিম সরবরাহ করতাম। সাপের ছড়াছড়ি, ঘরের ভিতরের চাল দিয়ে সাপ ঘুরে বেড়াতো। ঘরের চালের মধ্যে চড়ুই পাখি বাসা বাঁধতো। বাসা থেকে বাচ্চা বের করে প্রায়ই দেখতাম কত বড় হল। আবার বাসাতে ফিরিয়ে দিতাম। বাপ-মা চড়ুই ততক্ষণে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। রাতে ঘরের চালে ভুতুম পেঁচা আসতো ভুত ভুতুম করে ডাকতো। এদেরকে দেখে ইদুর দৌড়াদৌড়ি করতো। কিন্তু ঘুনাক্ষরে চিন্তা করিনি তারা ইঁদুর ধরতে এসেছে। মা বলতো ঘরের চালে হুতোম প্যাঁচার ডাকা অমঙ্গল। বাড়ির সামনে বাওড়ের পাড়ে মস্ত বড় ছাতিম গাছ ছিল। সেই গাছের খোড়লে বাসা বেধে ফেলল। বাচ্চা দিল। উড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বাচ্চারা কি কি করে তা দেখতাম। রাতের পাখিকে দিনে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তবে ভুতুম পেঁচাদের অমঙ্গলের বদনাম থাকলেও ইঁদুর মেরে মঙ্গল করে তা জানতে অনেক সময় পেরোতে হয়েছে।
বর্ষার আগে বর্ষা কালের জন্য জ্বালানি কাঠ সংরক্ষন করা হতো। এই জ্বালানি কাঠের মধ্যে সাপ এসে থাকতো। ছোটবেলায় আমাকে এই কাঠের মধ্য থেকে একবার সাপে কামড়েছিল। আমি প্রায় মরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার আব্বাকে তো দু-দুবার সাপে কামড়েছে তাও বাড়ির উঠান থেকে। বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হলেই সাপ চোখে পড়তো। বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে রাজগঞ্জ বাজার। বর্ষাকালে এ বাজারে যাওয়ার পথে এক গন্ডা সাপের সাথে দেখা হতো। সাপে ধরা ব্যাঙের আর্তনাদ কানে আসতো। পাতি শেয়ালের কোন অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ির এক কিলোমিটার উত্তরে আরো একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি লেক তার নাম ঝাপার বাওড়। তাই মাত্র দুদিক খোলা ছিল। খুব সকালে বা বিকালে ছাগলকে একা পেলেই পাতিশিয়ালরা ধরতো। একটানে নাড়িভুড়ি বের করে ফেলার দৃশ্য দেখেছি। তবে প্রথমে ঘাড়ে কামড় দিয়ে কাবু করে ফেলতো। যেটা এখন আমরা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে বাঘ বা সিংহকে করতে দেখি। মানুষের সামনে ধরতে দ্বিধা করতো না। মানুষকে অনেক সময় কামড় দেওয়ার জন্য দল বেধে ধাওয়া করত। আমিও এমন পরিবেশে পড়েছি। কুকুর শেয়ালকে ধাওয়া দিত। শেয়ালগুলো রাতে এসে কুকুরের বাচ্চার ধরে নিয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো কুকুর ছিল। শীতকালে কুকুরের অনেকগুলো বাচ্চা হত। তখন খেজুরের রস থেকে গুড় করার জন্য চুলা যাকে আমরা বাইন বলি তার পিঠের পাশের ছাইয়ের ভিতর ঘুমাতো। আমরা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে খেলা করা পছন্দ করতাম। অনেকদিন কুকুরের বাচ্চা বানের আগুনের ভিতর পড়ে পুড়ে মারা যেত অথবা বাড়ির কেউ তাড়াতাড়ি তুলে ফেলার জন্য বেঁচে যেত বা গুরুতর আহত হত। আমরা খুব কষ্ট পেতাম, আদর-যত্ন করতাম। গুড় জাল দেওয়া শেষ হলে বিচ মারা হতো। খেজুরের গাছের পাতার ডাগো দিয়ে কাঠি বানিয়ে জাল দেওয়া পাত্র জালোর ভিতর ঘষে গুড়ের সাথে মিশিয়ে দিলে crystal তৈরি হতো। সেই crystal গুড়ের সাথে মিশিয়ে দিলে শক্ত হয়ে যেত। এরপর ‘জালো’র গায়ে লেগে থাকা গুড় তালপাতা ভাঁজ করে বা আঙুল দিয়ে মজা করে চেঁচে চেঁচে খেতাম। তার একটা আলাদা সুগন্ধ ছিল তখনকার দিনের একমাত্র মিষ্টি, গুড় ভরসা। বীচ মারা গুড় কলা পাতার ওপর বিছিয়ে দিয়ে ঠান্ডা ও শক্ত করে পাটালি তৈরি করা হতো। কোন কোন সময় নারকেল গুড়ের ভিতরে দিয়ে নারকেলের পাটালি তৈরি করা হতো। মাসের পর মাস এই পাটালি সংরক্ষণ করে খাওয়া হতো। তখনকার দিনে এভাবেই সংরক্ষণ করা হতো। আমাদের ফ্রিজ থাকা তো দূরের কথা চিন্তাই ছিলনা। বর্ষার সময় পাটালি গুড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। একটানা কয়েকদিন বৃষ্টি হলে হাটে যাওয়া যেত না। কোন ব্রিজ ছিলনা, কোথাও কোথাও দু’একটি কালভার্ট ছিল তাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকতো। পাড়ার সবার ছাতা ছিল না। তবে গরীব মানুষের এক ধরনের মাথালি ব্যবহার করত যা ছন বা গোলপাতা দিয়ে তৈরি করা হতো। তখনকার দিনে পলিথিন এখনকার মতো সহজলভ্য ছিল না। যার মাথালি ছিল না সে বরং মান কচুর পাতা মাথার উপর ধরে চলাচল করত। এটাই ছিল আমাদের গ্রামের জীবন।
 বর্ষার শুরুতে বৈশাখ মাসে ঢল আসলে হড়খালি এবং বেনাখালি এই দুই খাল দিয়ে মাছ উজানে উঠতো। মাছ কিজন্য এই বর্ষাকালে পাগলের মত উজান স্রোতে উঠতো তা জানতাম না।
বর্ষার শুরুতে বৈশাখ মাসে ঢল আসলে হড়খালি এবং বেনাখালি এই দুই খাল দিয়ে মাছ উজানে উঠতো। মাছ কিজন্য এই বর্ষাকালে পাগলের মত উজান স্রোতে উঠতো তা জানতাম না।
 হড়খালী সামনে আমন ধানের পানি ভর্তি ক্ষেতে মাছ জাহাজের মতো মাথায় পানি নিয়ে দৌড়ে বেড়াতো। খেপলা জাল নিয়ে তার পিছনে হাটু পানিতে সবাই দৌড়ে দৌড়ে জাল ফেলতো। ওদিকে খাল দিয়ে পানি নেমে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে মাছ উঠছে। সেখানে ধোড়া সাপ গাছের শিকড়ে শরীর পেঁচিয়ে মাছ ধরার জন্য ওৎ পেতে থাকতো। নিচে খালে পাটা বা বানা দিয়ে মাছ চলার রাস্তা আটকে দিত। পাটার ওপর দিয়ে জাল মেলে দেওয়া থাকতো। মাছ পাটায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে লাফ দিয়ে জালের উপর পড়তো। পাটার দুই প্রান্তে স্রোত কম থাকত, সেখানে উল্টা দিকে মুখ করে দোয়াড় পাতা থাকতো তার ভিতর মাছ ঢুকে আটকে যেত। উল্টো স্রোতে কিভাবে মাছ আসতে পারে এটা আমার মনে দাগ কেটেছিলো। সারা জীবন উল্টো স্রোতে চলেছি। ক্লান্ত হয়নি।
হড়খালী সামনে আমন ধানের পানি ভর্তি ক্ষেতে মাছ জাহাজের মতো মাথায় পানি নিয়ে দৌড়ে বেড়াতো। খেপলা জাল নিয়ে তার পিছনে হাটু পানিতে সবাই দৌড়ে দৌড়ে জাল ফেলতো। ওদিকে খাল দিয়ে পানি নেমে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে মাছ উঠছে। সেখানে ধোড়া সাপ গাছের শিকড়ে শরীর পেঁচিয়ে মাছ ধরার জন্য ওৎ পেতে থাকতো। নিচে খালে পাটা বা বানা দিয়ে মাছ চলার রাস্তা আটকে দিত। পাটার ওপর দিয়ে জাল মেলে দেওয়া থাকতো। মাছ পাটায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে লাফ দিয়ে জালের উপর পড়তো। পাটার দুই প্রান্তে স্রোত কম থাকত, সেখানে উল্টা দিকে মুখ করে দোয়াড় পাতা থাকতো তার ভিতর মাছ ঢুকে আটকে যেত। উল্টো স্রোতে কিভাবে মাছ আসতে পারে এটা আমার মনে দাগ কেটেছিলো। সারা জীবন উল্টো স্রোতে চলেছি। ক্লান্ত হয়নি।
সেকাল বর্ষা শুরুতে বৈশাখে ঢল নামত। চারিদিকে থৈ থৈ ঠান্ডা পানি গর্তে ঢুকে যেতো। চারিদিকে পানি সাপের আর যাওয়ার জায়গা নেই। কিংবা বেরনোর সময় পায়নি। কিংবা প্রিয় আস্তানা ছেড়ে যেতে চায় না। আব্বা আমাকে সাথে নিয়ে মাঠে যেতো পানি ধরে রাখার জন্য আইলের ধারের গর্ত বন্ধ করা দরকার হতো। এই গর্ত বন্ধ করতে গিয়ে দেখতাম কিছুক্ষণ পরপর কি যেন উপরে উঠে দম নিচ্ছে তারপর আবার পানির ভেতর ডুবে যাচ্ছে। আসলে ওটা একটি সাপ তার গর্তে পানি তাই উপরে এসে দম নিয়ে আবার পানির নিচে চলে যাচ্ছে। বিষধর সাপ, আব্বা সতর্ক করতেন। কোদাল সাথে নিয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ কোদাল ধরে চুপটি করে দাড়িয়ে থাকতেন। সাপ দম নিতে উঠলে এক কোদালের কোপে ঘাড় কেটে দিতেন। ৪-৫ ফুট লম্বা সাপ লাফ দিয়ে কামড় দিতে পারে তাই সাবধান থাকতে হতো। কাদার গর্তের ভেতর মাথা কেটে দেওয়ার পরও টানাটানি করে দেখেছি টেনে বের করা যায় না। তখন যদিও এর ম্যাকানিজম বুঝতাম না। পরবর্তীকালে বুঝেছি শরীরটা বাকিয়ে দিয়ে পেটের আশটেগুলো গর্তের গায়ে চেপে ধরে একসাথে অনেক শক্তি সৃষ্টি করতে পারতো। প্রকৃৃতি যে কি রহস্যময় তা একটি বিষয় পৃথকভাবে চিন্তা করে বোঝা যায় না। বাওড়ের ভেতর এক ধরনের সাপ ছিল এটাকে কাচো সাপ বলে। এটা বৃষধর সাপ না, জীবনের প্রায় পুরোটা সময় পানির ভেতর থাকে, পানির উপরে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। ডিম পাড়ে না, বাচ্চা দেয়। ছিটকে জাল বা ঠেলা জাল দিয়ে এক ক্ষেপণে ৪-৫ টা সাপ উঠতো।
বাওড়ে কচ্ছপের অভাব ছিল না। স্থানীয়ভাবে কচ্ছপকে ‘কচ্ছম’ বলে। শীতের দিনে কচ্ছপ ডাঙ্গায় উঠে রোদ পোহাতো। কোনো কোনোটা বিশাল আকারের। গায়ে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ থাকতো। এগুলোকে স্থানীয়ভাবে ঢালেন কচ্ছপ বলত। বর্ষার দিনে বাতাসে বাওড়ের পাড় পর্যন্ত কচুরিপানা আসতো। একদিন পানি আর কচুরিপানার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। ডান পায়ের সামনের দিকের ভাজে কিসে পানির ভিতর কামড়ে ধরল, দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পা নাড়াতে পারলাম না। ভারী কোন জন্ত কামড়ে ধরেছে। তাই সাংঘাতিক রকমের ভয় পেয়ে গেলাম। ধরে নিয়েছিলাম পানির ভিতর কচুরিপানার ভেতরে সাপে কামড় দিয়েছে। কিন্তু কিছু পেঁচিয়ে ধরলো না। পিচ্ছিল একটা লাঠির মত পায়ে ঘষা লাগলো। মনে করলাম বড় একটা সাপে কামড়ে ধরেছে। এরপরে পায়ে বড় একটা চাকার মত বস্তু ঠেকলো। বুঝতে দেরী হলো না কচ্ছপ কামড়িয়েছে। টানাটানি করে পা ছাড়ালাম, রক্ত বের হচ্ছে। অনেকগুলো ছোট ছোট দাঁত দিয়ে কমড়ানোয় বড় আকারের কোন জখম হয়নি।
একদিন পাশের ঘরে ঘরে শুয়ে আছি। এখন আর সে ঘর নেই। এখনও টিকে থাকা উত্তরের দিকে ঘরের মতো এটিও বড় চৌচালা ঘর ছিল। চালের ভিতর দিকে সবসময় সাপ উৎপাত করত। সেদিন একটা সাপ যেতে যেতে একটা বাঁশের পাড় এর ফাকের ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমি একটা মওকা পেয়ে গেলাম। চালে গোজা একটি কাচি হাতে নিলাম। কাঁচি দিয়ে সাপের লেজ ধরে একটানে মাঝখান থেকে কেটে ফেললাম। কিন্তু সামান্য একটু চামড়া যুক্ত ছিল। সে বাশের খোলের ভিতর থেকে মুখ ফিরিয়ে এই অবস্থায় আমাকে একটা কামড় বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। যাহোক আমি সতর্ক ছিলাম তাই বিষধর সাপটি কামড়াতে পারেনি। স্থানীয়ভাবে এই সাপকে কান্দল সাপ বলে।
আমাদের বাড়ির আশপাশে যেখানে ভাঙা ইট গাদা দেয়া থাকতো সেখানে চেলা বিচ্ছুর কোনো অভাব ছিলনা। আমাদের ঘরের মধ্যেও মাঝে মধ্যে পাওয়া যেত। হলুদ রঙের চেলাগুলোকে সবাই পাকা চেলা বলতো। এগুলো বেশ বিষাক্ত, কামড়ালে ফুলে ওঠে, অনেকদিন পর্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। ২০০৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার শিউলে নুতন একটা অভিজ্ঞতা হল। ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি নুতন কিছু আছে কিনা দেখার এবং ফটো তোলার চেষ্টা করছি। এমন সময় দেখলাম হলুদ পাকা চেলা শুকিয়ে রাবার ব্যান্ড দিয়ে তাড়ি বেঁধে রেখেছে। পাশে একটা মেশিন, খদ্দের আসলে এর ভিতরে ঢুকে ঘুরিয়ে পাউডার বের করছে। একটা কাঠি দিয়ে এই পাউডার আর একটা বাটিতে মধু মাখিয়ে রাস্তার মানুষকে খাওয়াচ্ছে। আজব ব্যাপার? চেলা শুকিয়ে গুঁড়ো করে খায় একথা জানা তো দূরের কথা, ভাবনার বাইরে। যাহোক ফটো তোলার চেষ্টা করলাম। সে মারমুখী হল ফটো তোলা হলো না। এরপর যতবার গিয়েছি। যেকোনো একজন চেলাওয়ালাকে খুঁজেছি,পাইনি। এখন ধনী দেশ গাড়ি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এইসব নিয়ে ব্যস্ত চেলা ধরার সময় কই।